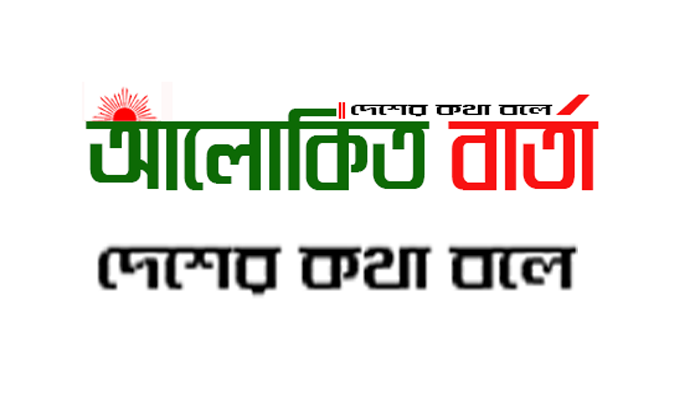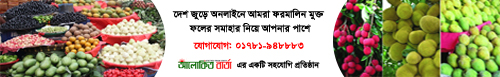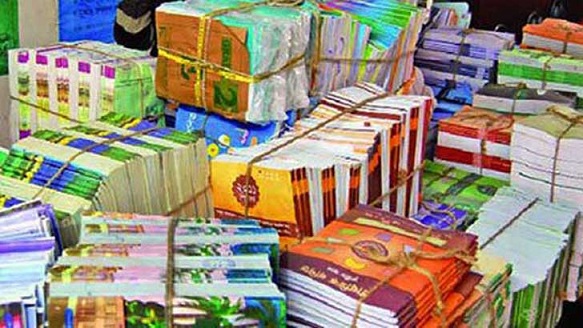জেলেদের দারিদ্রতার কারনে বিপন্ন হচ্ছে নদী-সাগরের ইলিশ



রেদওয়ান শাওন ।।সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বরিশাল বিভাগের বিভিন্ন নদী তীরের জেলেরা সংসারের অভাব মেটাতে কোনো উপায় না পেয়ে মাছ ধরতে নদীতে যেতে বাধ্য হচ্ছে। এদিকে নয়ন নামের এক জেলে বলেন মাত্র নয় বছর বয়সে বাবার হাত ধরে মাছ ধরতে নদীতে যাওয়া শুরু হয়েছিল আমার। ৪১ বছর ধরে বিভিন্ন নদীর বুকে মাছ ধরছেন তিনি। অথচ সংসারের অভাব মেটাতে আজও তাকে লড়াই করতে হচ্ছে। তিনি বলেন বেঁচে থাকার জন্য আমরা নিত্য সংগ্রাম করে যাচ্ছি, এই সংগ্রাম কেবল কয়েক দিন বা রাতের নয়, আমরা দিনের পর দিন এই সংগ্রাম করে যাচ্ছি। আসলে আমার মনে হচ্ছে জেলে হয়ে জন্মানোটা ছিলো এক ধরনের অভিশাপ। প্রতিবেদকের কাছে এভাবেই নিজেদের কষ্টের কথা তুলে ধরেন নয়ন ও নদীকুলের জেলেরা। বরিশাল বিভাগের ৬টি জেলায় তার মতো আরো প্রায় ৪০০,০০০ জেলে রয়েছে যাদের অবস্থা প্রায় একই রকম। বরিশালের পোর্টরোডে এক কেজি ইলিশ বিক্রি হয়েছে ৬-৮ শত টাকায়।
কিন্তু বরিশাল, ভোলা, বরগুনা,ঝালকাঠী,পটুয়াখালী,পিরোজপুরসহ বিভিন্ন ছোট বড়ো নদীকুলের জেলেরা মাসিক ৬,০০০– ৮,০০০ টাকা উপার্জন করতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে দিন-রাত। নদী ও সাগরে যেসব মাছ পাওয়া যায় তার মধ্যে ইলিশ হচ্ছে অন্যতম। উচ্চ পুষ্টিগুন ও অর্থনৈতিক মূল্য ছাড়াও বাঙালী সংস্কৃতিতে এই মাছটির রয়েছে আলাদা স্বকীয়তা। সারা বাংলাদেশে প্রায় ১১ লাখেরও বেশি উপকূলীয় মৎসজীবি সরাসরি এই মাছটি ধরার সঙ্গে জড়িত। অন্যদিকে মাছের বিপনন, পরিবহন ও বাজারজাতকরণের সঙ্গে যুক্ত আছে আরো প্রায় ৩০ লাখ মানুষ। কিন্তু বেসরকারী সংস্থা ওয়ার্ল্ড ফিশ-এর তথ্য মতে, নদীতে ইলিশের পরিমান কমছে প্রতিনিয়ত, মারাত্বক ঝুঁকির মুখে রয়েছে বাঙালীর সবচেয়ে প্রিয় এই মাছ। এর মূল কারণ হচ্ছে পলি জমে তলদেশ ভরাট হয়ে নদীর গভীরতা কমে যাওয়া এবং মাত্রাতিরিক্ত জাটকা (ইলিশের পোনা) নিধন। গত ২০০৫-০৬ অর্থবছরে বাংলাদেশে ইলিশের উৎপাদন ছিল ২২০,০০০ মেট্রিক টন, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মাছটির উৎপাদন ছিল ৩৮৭,০০০ মেট্রিক টন, অর্থাৎ দশ বছরে এর উৎপাদন বৃদ্ধির হার ৮৫% হয়েছে। আলোকিত বার্তাকে এই তথ্য জানিয়েছেন বাংলাদেশ মৎস্য অধিদপ্তরে’র কর্মকর্তা। তবে নদী জুড়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি হলেও ভাগ্যের তেমন উন্নতি হয়নি এদেশের জেলে সম্প্রদায়ের। চরম অভাবের সময় একটু বেশি আয়ের আশায় অনেক সময়ই আইন অমান্য করে অনেক জেলে নদীতে জাটকা ধরতে বের হন। সত্য বলতে কি, অভাবের তাড়নায় অনেক সময় এই অন্যায়ের পথ বেছে নিতে বাধ্য হন অনেক জেলেরা। এদিকে বরিশাল চন্দ্রোমোহনের সেলিম মিয়া ও দুলাল শেখ বলেন, আমরা খুব ভালো করেই জানি যে জাটকা নিধন আইনত অবৈধ ও দন্ডণীয় জানা সত্বেও আমাদের মধ্যে অনেকেই এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে নদীতে মাছ ধরে থাকে। আমরা জাটকা ধরার নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করে নদীতে মাছ ধরতে যাই। কারন সেসময় আমাদের কোনো কাজ থাকে না। উপার্জনের অন্যান্য রাস্তাও বন্ধ থাকে। আর মহাজনরাও আমাদের ঋণের টাকা শোধ করার জন্য চাপ দিতে থাকে। মাঠপর্যায়ে বাস্তবতা বেশিরভাগ জেলেরই নিজের কোনো জাল বা নৌকা নেই। তারা নৌকা ও জালের টাকা জোগাড় করেন স্থানীয় মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে। তাই জাল, নৌকা এমনকি ধৃত মাছের উপরেও মহাজনদের পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকে। দরিদ্র জেলেরা সবসময়ই মহাজন বা ব্যাপারীদের দ্বারা শোষিত হয়। ব্যাপারীদের কাছে আমরা যে দামে মাছ বিক্রি করি, খোলা বা পাইকারী বাজারে প্রকৃতপক্ষে সেই মাছের দাম অনেক বেশি। আমরা কখনই মাছের প্রকৃত মূল্য পাই না, একথা বলেছেন জেলে আব্দুল সাত্তার। সাধারণত জেলেরা কখনই পাইকারী ও খূচরা বিক্রেতা এবং ভোক্তাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করেন না। তারা স্থানীয় ঘাটে ব্যাপারীদের কাছে মাছ বিক্রি করেন। জেলেদের কাছ থেকে এই মাছ সংগ্রহে মধ্যস্থতা করে স্থানীয় আড়তদার। এরা নিলাম মূল্যের ২–৫ শতাংশ অর্থ কমিশন হিসেবে নিয়ে থাকে। ঘাটের এই নিলামকারী, আড়তদার ও ব্যাপারীরাই আসলে খোলা বাজারে ইলিশের মূল্য নির্ধারনে মূল ভূমিকা রাখেন। এই বৃত্তের সর্বনিন্ম পর্যায়ে রয়েছে জেলেরা যারা কখনই নিজেদের ইচ্ছায় মাছের মূল্য নির্ধারন করতে পারে না। বেসরকারী সংস্থা কোষ্ট ট্রাষ্ট অনেক দিন ধরেই ভোলা জেলায় জেলেদের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। সংস্থাটির কর্মসূচি সমন্বয়ক বলেন, গড়ে প্রতিটি জেলে পরিবারের ঋণের পরিমান ৬২,০০০ টাকা। পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি) পরিচালিত এক গবেষনা প্রতিবেদনের তথ্য তুলে ধরে তিনি বলেন, ভোলার ৩৩% জেলের নিজস্ব কোনো বসতভিটা নেই, প্রায় ৪০% জেলের কোনো নৌকা নেই এবং ২৯% জেলের কোনো মাছ ধরার জাল নেই, তাই কাজে আসছে না সহায়তা প্রকল্প।
ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসুচির আওতায় দেশের ক্ষতিগ্রস্থ্য জেলেদের বিভিন্ন ধরনের সহায়তা প্রদান করে আসছে। এই সহায়তা প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে জাটকা ও মা ইলিশের মৌসুমে জেলেদের মাছ ধরা থেকে বিরত রাখা যায়। বছর জুড়ে মূলত চার মাস এই ধরনের নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়ন করে সরকার। এদিকে ভোলা জেলার কেন্দ্রীয় মৎসজীবি সমবায় সমিতি’র সম্পাদক বলেন বর্তমানে ভোলা জেলায় প্রকৃত জেলের সংখ্যা ২০০,০০০ এর বেশি যারা ইলিশ ধরার সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত। কিন্তু এদের মধ্য থেকে সরকারিভাবে মাত্র ১১৭,০০০ জনকে মৎসজীবি হিসেবে নিবন্ধিত করেছে। অথচ নিবন্ধিত অনেকেই মাছ ধরার সঙ্গে জড়িত নয়। স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা ভোট পাওয়ার জন্য প্রকৃত জেলেদের বাদ দিয়ে অনেক অপেশাজীবিকে জেলে হিসেবে নিবন্ধিত করেছে। তার মতে, সরকারের পক্ষ থেকে দরিদ্র জেলেদের খাদ্য সহায়তা দেয়া হয় তা আসলে কোনো উপকারে আসছে না। তিনি বলেন, সরকারের এই কর্মসুচির আওতায় প্রতিটি পরিবারের ১৬০ কেজি করে চাল পাওয়ার কথা থাকলেও প্রকৃতপক্ষে তারা পাচ্ছেন মাত্র ৬০-৭০ কেজি চাল। দূর্নীতির অভিযোগ করে তিনি বলেন, সরকারের দেয়া সহায়তার এই চাল একজন জেলে হাতে পায় মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞা মৌসুমের অনেক পরে। এমনিতেই জাটকা ও ইলিশের ডিম পাড়ার মৌসুমে মাছ ধরার উপরে নিষেধাজ্ঞা থাকায় জেলেদের ওই সময়ে কোনো উপার্জন থাকে না। অন্যদিকে সরকারের পক্ষ থেকে যে সহায়তা দেয়া হয় তাও সময়মতো হাতে পাওয়া যায়না। ফলে পরিবারের সদস্যদের খাদ্যের যোগান দিতে বাধ্য হয়ে অনেক জেলেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মাছ ধরতে যায়। তখন বাধ্য হয়ে তারা মহাজন/ব্যাপারীদের কাছ থেকে টাকা ঋণ নিয়ে সংসার চালান। এদিকে জেলে আব্দুল সাত্তার বলেন, আমাদের অর্থ বা খাদ্য সহায়তার প্রয়োজন নেই। বরং আমাদের বিকল্প কর্মসংস্থান কিংবা মৌসুমী ব্যবসার জন্য প্রশিক্ষণ বা অর্থ সহায়তা প্রদান করুন যাতে আমাদের দৈনন্দিন একটি উপার্জন হয়। সামনে আশার আলো, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে মাত্রাতিরিক্ত ইলিশ নিধন বন্ধে সরকার এরই মধ্যে নানা কর্মসুচি গ্রহন করেছে। হিলশা কনজারভেশন ট্রাষ্ট ফান্ড (এইচসিটিএফ) নামে একটি প্রকল্প চালুর মাধ্যমে সরকার ইলিশ সংরক্ষরনের পাশাপাশি জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করছে। মৎস অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের দেয়া তথ্য মতে, ইলিশ ব্যবস্থাপনায় একটি তহবিল তৈরির লক্ষ্যে যুক্তরাজ্যের ডারউইন ইনিশিয়েটিভ বাংলাদেশ সরকারকে সহায়তা প্রদান করবে। ডারউইন ইনিশিয়েটিভের আওতায় এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে মেঘনাসহ দক্ষিনাঞ্চলের বিভিন্ন নদী ও সাগরে ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি করা। এবিষয়ে বাংলাদেশ মৎস্য অধিদপ্তরে’র মহা-পরিচালক বলেন, ইলিশ সংরক্ষনে ট্রাষ্ট ফান্ড গঠন করা গেলে জাটকা মৌসুমে জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা যাবে।